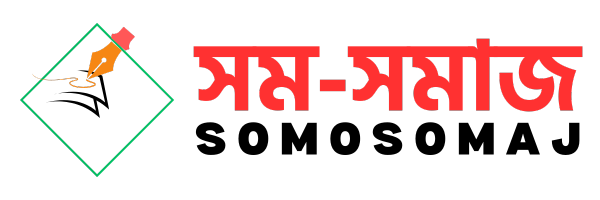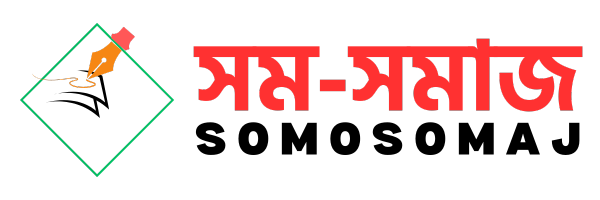এক
এক অদ্ভুত আর্তি যেন ঝরে পড়ছে বাংলাদেশের প্রতিটি রান্নাঘর থেকে। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে স্বস্তির সুবাতাস, যখন সয়াবিন আর পাম তেলের দাম গত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছোঁয়ার পথে, তখন আমাদের দেশের বাজারে ঠিক উল্টো চিত্র। দাম কমার বদলে উল্টো বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কেন এই বৈপরীত্য? ব্যবসায়ীরা ডলারের দাম বৃদ্ধি আর ব্যাংকিং জটিলতার অজুহাত দিচ্ছেন, কিন্তু ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলো একে নিছক অজুহাত বলেই উড়িয়ে দিচ্ছে, তাদের হিসাবে প্রতি লিটারে ব্যবসায়ীদের পকেটে যাচ্ছে অন্যায় মুনাফা।
আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও সেই সুফল যখন ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায় না, বিশেষ করে দাম কমার চেয়ে দাম বাড়ার খবর যখন দ্রুত কার্যকর হয়, তখন অর্থনীতিবিদরা একে বলেন অ্যাসিমেট্রিক প্রাইস ট্রান্সমিশন। এটি অনুসারে কাঁচামালের দাম বাড়লে উৎপাদক বা বিক্রেতারা খুব দ্রুত সেই বাড়তি খরচ পণ্যের দামে যোগ করে দেন, যেন রকেটের গতিতে দাম বাড়ে। কিন্তু কাঁচামালের দাম কমলে সেই সুবিধাটুকু ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে গড়িমসি করা হয়, দাম কমে কচ্ছপের গতিতে, অথবা কমেও না অনেক সময়। এই ধারণাটি আমাদের ভোজ্যতেলের বাজারের বর্তমান অবস্থার সাথে যেন হুবহু মিলে যায়। যখন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম চড়া ছিল, ব্যবসায়ীরা এক মুহূর্তও দেরি করেননি দেশের বাজারে দাম বাড়াতে। কিন্তু এখন দাম তলানিতে নেমে এলেও ডলার, ব্যাংক, শুল্ক ইত্যাদি নানা কারণ দেখিয়ে দাম কমানোর বদলে উল্টো বাড়ানো হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায়, যেমন ARDL (Autoregressive Distributed Lag) এবং NARDL (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag) মডেল ব্যবহার করে করা বিশ্লেষণেও দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির (positive shock) প্রভাব স্থানীয় বাজারে খুব দ্রুত পড়ে, কিন্তু মূল্যহ্রাসের (negative shock) প্রভাব পড়ে অনেক ধীরে বা আংশিক, যা বাজারের স্বাভাবিক ছন্দ নষ্ট করে দেয়।
এই পরিস্থিতির পেছনে আরেক বড় কারণ বাজারের কাঠামো। বাংলাদেশের ভোজ্যতেলের বাজার মূলত নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটি বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীর দ্বারা – মেঘনা, সিটি, টিকে গ্রুপসহ মাত্র পাঁচ-ছয়টি প্রতিষ্ঠান সিংহভাগ বাজার দখল করে রেখেছে। অর্থনীতিতে এই অবস্থাকে বলা হয় অলিগোপলি। এই ধরনের বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় তাদের মধ্যে এক ধরনের অলিখিত বোঝাপড়া তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকে। পল সুইজি তার কিংকড ডিম্যান্ড কার্ভ মডেলে দেখিয়েছেন, অলিগোপলি বাজারে দাম সহজে কমতে চায় না। কারণ, কোনো একটি প্রতিষ্ঠান যদি দাম কমায়, প্রতিযোগীরাও সঙ্গে সঙ্গে দাম কমিয়ে দেবে নিজেদের বাজার ধরে রাখতে। ফলে দাম কমানো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা তেমন বাড়বে না। অন্যদিকে, কেউ যদি দাম বাড়াতে চায়, প্রতিযোগীরা সাধারণত সেই পথে হাঁটে না, ফলে দাম বাড়ানো প্রতিষ্ঠানের বিক্রি কমে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এই উভয় সংকটের কারণে দাম একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে থাকার প্রবণতা দেখা যায়, বিশেষ করে নিচের দিকে নামতে চায় না। বাংলাদেশের ভোজ্যতেল বাজারেও এই চিত্র স্পষ্ট। গুটিকয়েক আমদানিকারক ও পরিশোধক মিলে বাজারের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করায় আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমলেও স্থানীয় বাজারে তার প্রতিফলন ঘটছে না, বরং সুযোগ বুঝে দাম বাড়িয়েই নেওয়া হচ্ছে।
সমস্যাটিকে কেবল স্থানীয় বাজারের নিরিখেদেখলে চলবে না, এর শিকড় প্রোথিত থাকতে পারে বিশ্ব অর্থনীতির কাঠামোগত বিন্যাসেও। আন্দ্রে গুন্ডার ফ্র্যাঙ্কের ডিপেন্ডেন্সি থিওরি বা আসক্তি তত্ত্ব এবং ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইনের ওয়ার্ল্ড-সিস্টেমস থিওরি অনুযায়ী, বিশ্ব অর্থনীতি একটি অসম কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে কিছু উন্নত দেশ (কেন্দ্র বা কোর) তাদের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতার জোরে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে (প্রান্ত বা পেরিফেরি) শোষণ করে নিজেদের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে। এই তাত্ত্বিক কাঠামো অনুযায়ী, বাংলাদেশ বা এই ধরনের প্রান্তীয় অর্থনীতির দেশগুলো বিশ্ববাজারের নানা সুযোগ, যেমন আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার সুবিধা পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না। কাঠামোগত দুর্বলতা, উন্নত দেশ বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর প্রভাব এবং স্থানীয় শক্তিশালী গোষ্ঠীর যোগসাজশে বিশ্ববাজারে দাম কমার সুফল প্রান্তিক দেশগুলোর সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর আগেই হারিয়ে যায় বা সীমিত হয়ে পড়ে। যেমন প্রান্তীয় দেশগুলোর প্রায়শই অপর্যাপ্ত অবকাঠামো (যেমন বন্দর, পরিবহন, গুদামজাতকরণ ব্যবস্থা), অদক্ষ সরবরাহ শৃঙ্খল বা সাপ্লাই চেইন, দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আমদানিনির্ভরতা থাকে। বিশ্ববাজারে দাম কমলেও এই দুর্বলতার কারণে পণ্য দেশে আনতে ও বিতরণ করতে অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় হয়, যা মূল্যের সুবিধাটুকু কমিয়ে দেয়। তাছাড়া, দর কষাকষির সক্ষমতা কম থাকায় আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কাছ থেকে সবসময় সবচেয়ে সুবিধাজনক দামে পণ্য কেনা সম্ভব হয় না। এদিকে উন্নত দেশ বা তাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কাঁচামাল কেনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শিপিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলো নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখে। বিশ্ববাজারে দাম কমলেও তারা তাদের মুনাফার মার্জিন ঠিক রাখতে বা বাড়াতে প্রান্তীয় দেশগুলোতে সেই অনুপাতে দাম কমায় না। তারা নানা রকম বাণিজ্য কৌশল ও চুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের লাভ নিশ্চিত করে। আবার প্রান্তীয় দেশগুলোতে প্রায়শই কিছু শক্তিশালী আমদানিকারক, ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্ববাজারে দাম কমলেও তারা নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে, মানে কার্টেল গঠন করে স্থানীয় বাজারে দাম কমায় না বা খুব সামান্য কমায়। তারা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, মজুদ করে রেখে দাম বাড়িয়ে দেয় এবং বিশ্ববাজারের মূল্য হ্রাসের সুবিধাটুকু নিজেরাই মুনাফা হিসেবে আত্মসাৎ করে। এই গোষ্ঠীগুলোর সাথে অনেক সময় নীতি নির্ধারকদেরও অনৈতিক সম্পর্ক থাকতে পারে, যা তাদের এই কাজ সহজ করে দেয়। ভোজ্যতেলের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটা অস্বাভাবিক নয়, যেখানে বৈশ্বিক মূল্যহ্রাসের সুবিধাটুকু নানা অজুহাতে বা প্রক্রিয়ার মারপ্যাঁচে ভোক্তা পর্যন্ত গড়াতে দেওয়া হচ্ছে না।
ব্যবসায়ীরা ডলারের মূল্যবৃদ্ধিকে একটি প্রধান কারণ হিসেবে দাঁড় করাচ্ছেন। অবশ্যই এক্সচেঞ্জ রেইট পাস-থ্রু এর ধারণা অনুসারে টাকার অবমূল্যায়ন বা কারেন্সি ডেপ্রিসিয়েশন হলে আমদানি খরচ বেড়ে যায়। এক্সচেঞ্জ রেইট পাস-থ্রু এর ধারণাটি বলে, টাকার অবমূল্যায়ন ঘটলে আমদানিকারকদের একই পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন ডলার) কিনতে আগের চেয়ে বেশি টাকা খরচ করতে হয়, যার ফলে আমদানিকৃত পণ্যের প্রাথমিক ব্যয় বেড়ে যায়। এই বর্ধিত আমদানি খরচ পরবর্তীতে উৎপাদনকারী, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের হাত ঘুরে চূড়ান্ত ভোক্তা মূল্যে যুক্ত হয়, ফলে বাজারে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পায়। তবে গবেষণা দেখায়, এই পাস-থ্রু বা সঞ্চার প্রক্রিয়াটি সবসময় সম্পূর্ণ বা তাৎক্ষণিক হয় না। অনেক সময় বিনিময় হারের বৃদ্ধি যতটা দ্রুত পণ্যের দামে প্রভাব ফেলে, বিনিময় হার কমলে বা স্থিতিশীল হলে সেই সুবিধাটা একই গতিতে ভোক্তা পায় না, যা আবার সেই অ্যাসিমেট্রিক প্রাইস ট্রান্সমিশনের ধারণাটিকেই সমর্থন করে। এছাড়া, এক্সচেঞ্জ রেইট পাস-থ্রু শুধুমাত্র বিনিময় হারের ওপর নির্ভর করে না, এটি দেশের মুদ্রানীতি, বাজারের প্রতিযোগিতা এবং বৈশ্বিক পণ্যের মূল্যের সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপরও নির্ভরশীল। তাই ডলারের মূল্যবৃদ্ধিকে একমাত্র কারণ হিসেবে দেখানোটা সরলীকরণ, বিশেষ করে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম ডলারের মূল্যবৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে কমেছে। এটি একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
এর সাথে যুক্ত হয় “রেন্ট-সিকিং” এবং “রেগুলেটরি ক্যাপচার” এর মতো বিষয়গুলো। অ্যান ক্রুগার ও গর্ডন টুলক বলছেন, রেন্ট-সিকিং হলো এমন এক আচরণ যেখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনশীলতা বা উদ্ভাবনের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে রাজনৈতিক বা নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটিয়ে বাড়তি সুবিধা বা মুনাফা আদায় করে নেয়। যেমন – শুল্ক ছাড়ের জন্য তদবির করা, বা নীতিমালা এমনভাবে তৈরি করানো যাতে নিজেদের একচেটিয়া বা প্রায়-একচেটিয়া আধিপত্য বজায় থাকে। জর্জ স্টিগলার তার “ইকোনমিক থিওরি অফ রেগুলেশন”-এ দেখিয়েছেন কীভাবে যে শিল্প বা খাতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা তৈরি করা হয়, সেই সংস্থাই কালক্রমে ঐ শিল্পের প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর দ্বারা প্রভাবিত বা ‘কব্জা’ (Captured) হয়ে যেতে পারে। ফলে, নিয়ন্ত্রক সংস্থা জনস্বার্থের বদলে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করে নীতিমালা তৈরি বা প্রয়োগ করতে পারে। ভোজ্যতেলের বাজারে শুল্ক ছাড় দেওয়া বা প্রত্যাহার করার সাথে সাথে দামের তাৎক্ষণিক ওঠানামা, এবং বারবার একই কয়েকটি বড় কোম্পানির দাবির মুখে দাম সমন্বয় করার ঘটনাগুলো এই তত্ত্বগুলোর বাস্তব প্রতিফলন কি না, সেই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যখন দেখা যায়, শুল্ক পুনর্বহালের কারণে দাম লিটারে ২১ টাকা বাড়ার কথা বলে ব্যবসায়ীরা ১৪ টাকা বাড়িয়েও ‘লোকসান হচ্ছে’ বলে দাবি করেন, তখন সন্দেহের অবকাশ থেকেই যায়।
এই সম্মিলিত কারণগুলোর ফলাফল হলো – আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের দামে স্বস্তি ফিরলেও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও গভীর হচ্ছে। বাজারের নিয়ন্ত্রণ যখন গুটিকয়েক প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে, যখন বৈশ্বিক অর্থনীতির কাঠামোগত অসমতা স্থানীয় বাজারকে প্রভাবিত করে, যখন নীতি নির্ধারনী প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়িক স্বার্থের অতিরিক্ত প্রভাব থাকে এবং যখন মূল্য সঞ্চার প্রক্রিয়াটি অসমভাবে কাজ করে – তখন এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটাই হয়তো অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন বাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা কমিশনের কার্যকর ভূমিকা, নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং একটি সুষম আমদানি ও শুল্ক নীতি প্রণয়ন করা, যা শুধু ব্যবসায়ীদের স্বার্থ নয়, সাধারণ ভোক্তাদের স্বার্থও রক্ষা করবে। নইলে, বিশ্ববাজারে দাম কমার সুফলটুকু আমাদের কাছে অধরাই থেকে যাবে, আর বাড়তি দামের বোঝা নীরবে বয়ে বেড়াতে হবে এদেশের লক্ষ কোটি সাধারণ মানুষকেই।