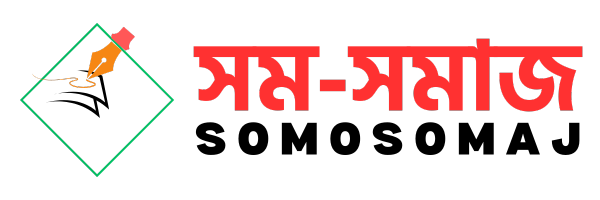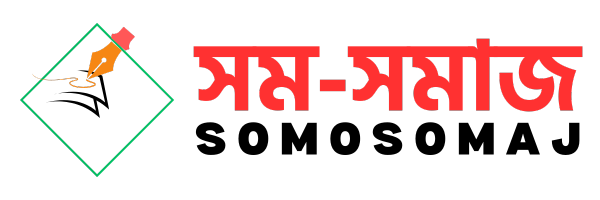কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়াতে ফকির লালন শাহের আখড়াবাড়িতে শিল্পী ফরিদা পারভীনের স্মরণসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ফরহাদ মজহার মন্তব্য করেন যে, “লালনের গানের সঙ্গে নাচ যায় না, এটা ক্ষতিকর”। তিনি আরও বলেন, “লালনের গান যে সাধকদের, বাংলার ভাব”। এই স্মরণসভাটি ফরিদা পারভীনের মৃত্যুর পর আয়োজিত হয়েছিল এবং লালন একাডেমি এটি আয়োজন করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরহাদ মজহার বলেন, ফরিদা পারভীন আমাদের প্রথমে দেখিয়েছেন যে লালনের গান শুধুই সংগীত নয়, এটি ভাবসংগীত। এটি বিশেষ দার্শনিক অবস্থানের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার একটি পদ্ধতি।
তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান আমলে লালনের গান মূলত পল্লিগীতি হিসেবে গাওয়া হতো, লালনের নাম উল্লেখ করা হতো না। স্বাধীনতার পরে এটি লালনের সংগীত হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে এসেছে। ফরিদা পারভীন তার গায়কির মাধ্যমে লালনের গানকে পল্লিগীতি থেকে ভাবগানের স্তরে নিয়ে গেছেন। লালনের গানকে কেবল শিল্পী হিসেবে দেখানো হলে তা অপমান, মন্তব্য করে ফরহাদ মজহার বলেন, এটি বাংলার ভাবচর্চা ও দর্শনচর্চার দীর্ঘ ধারার অংশ। তবে শিক্ষিত মহল এবং যারা লালনের গান চর্চা করেন, তাদের মধ্যেও এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান কম।
যারা বলেন লালনের গানের সঙ্গে নাচ ক্ষতিকর, তাদের যুক্তিগুলোকে যদি আমরা কেবল সারফেস লেভেলে বা উপরিতলে দেখি, তাহলে তিনটি প্রধান আপত্তির দেখা মেলে: সাধনার পবিত্রতা নষ্ট হওয়া, অর্থের সরলীকরণ ঘটা এবং সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা হারানো। এই যুক্তিগুলো শুনতে বেশ জোরালো এবং আপাতদৃষ্টিতে শিল্পের প্রতি গভীর মমতা থেকেই উৎসারিত বলে মনে হয়। কিন্তু বরফখণ্ডের চূড়া যেমন তার বিশাল ভিত্তিকে জলের নিচে লুকিয়ে রাখে, তেমনি এই আপত্তিগুলোর গভীরেও লুকিয়ে আছে এক জটিল মতাদর্শিক জগৎ। এই অধ্যায়ে আমরা সেই বরফখণ্ডের গভীরে ডুব দেব এবং দেখব, কীভাবে ‘পবিত্রতা’, ‘অর্থ’ এবং ‘ঐতিহ্য’-এর মতো ধারণাকে ব্যবহার করে শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় এবং মানবদেহকে করা হয় রাজনীতির বিষয়বস্তু।
‘পবিত্রতা’র ধারণা এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাস (Epistemological Hierarchy)
লালনের গানে নাচের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং আবেগপূর্ণ যুক্তিটি হলো ‘পবিত্রতা’ (Sanctity) রক্ষার যুক্তি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, লালনের গান এক আধ্যাত্মিক সাধনা, এক প্রকারের ধ্যান (Meditation), যা ইন্দ্রিয়ের জগৎ অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় সত্যের দিকে যাত্রার সঙ্গীতময় রূপ। আর ধ্যান মানেই শারীরিক স্থিরতা, মানসিক একাগ্রতা, জাগতিক কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা। অন্যদিকে, নাচকে দেখা হয় একটি জাগতিক, শারীরিক এবং প্রায়শই ইন্দ্রিয়-উত্তেজক ক্রিয়া হিসেবে। শরীর মানেই চঞ্চলতা, কামনা, বাসনা – অর্থাৎ যা কিছু আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী। সুতরাং, এই দুইয়ের মিশ্রণ আধ্যাত্মিকতাকে ‘অপবিত্র’ করবে, সাধনার পরিবেশকে ‘দূষিত’ করবে।
এই আপাত সহজ বিভাজনটি আসলে এক গভীর জ্ঞানতাত্ত্বিক স্তরবিন্যাসের (Epistemological Hierarchy) ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যা পাশ্চাত্য দর্শনের প্লেটোনিক (Platonic) এবং কার্তেসীয় (Cartesian) দ্বৈতবাদ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। প্লেটো মনে করতেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ হলো আদর্শ জগতের একটি অসম্পূর্ণ ছায়া মাত্র। প্রকৃত সত্য কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা বা যুক্তির মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, শরীরের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নয়। এই চিন্তারই আধুনিক রূপ দেন রেনে দেকার্ত (René Descartes), যিনি মন (Mind) বা আত্মা (Soul)-কে দেহ (Body) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দর্শনে, মন হলো যুক্তির উৎস, দর্শনের ক্ষেত্র, আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান – এক কথায়, মানবসত্তার বিশুদ্ধতম অংশ। অন্যদিকে, দেহ হলো কামনা-বাসনার আধার, নশ্বর এবং জ্ঞানের পথে একটি বাধা বা কারাগার মাত্র (Descartes, 1641)।
এই দেহ-বিরোধী দ্বৈতবাদ আমাদের সংস্কৃতিতে এতটাই গভীর প্রভাব ফেলেছে যে, আমরা প্রায়শই অবচেতনভাবেই একে সত্য বলে ধরে নিই। এর ফলে এক ধরনের সাংস্কৃতিক স্তরবিন্যাস তৈরি হয়, যেখানে যা কিছু মানসিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক (যেমন – গান শোনা, কবিতা পাঠ, দর্শন আলোচনা), তা ‘উচ্চ সংস্কৃতি’ (High Culture) হিসেবে গণ্য হয়। আর যা কিছু শারীরিক (যেমন – নাচ, খেলাধুলা, কায়িক শ্রম), তা ‘নিম্ন সংস্কৃতি’ (Low Culture) হিসেবে বিবেচিত হয়।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে, লালনের গানের সঙ্গে নাচকে মেশানোটা হলো ‘উচ্চ’ সংস্কৃতির সঙ্গে ‘নিম্ন’ সংস্কৃতিকে মিলিয়ে ফেলার মতো একটি গর্হিত কাজ। এটি যেন মন্দিরের পবিত্র গর্ভগৃহে বাজারের কোলাহলকে আমন্ত্রণ জানানোর সামিল। এই শুদ্ধাচারী (Puritanical) মানসিকতা কেবল লালন আর নাচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শিল্প-সাহিত্যের বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়। যেমন, অনেকেই মনে করেন সিরিয়াস সাহিত্যের চলচ্চিত্র রূপায়ণ সাহিত্যের গভীরতাকে নষ্ট করে দেয়, কারণ চলচ্চিত্র একটি ‘ভিজ্যুয়াল’ বা ইন্দ্রিয়নির্ভর মাধ্যম, যা নাকি সাহিত্যের বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতাকে ধারণ করতে অক্ষম। এই মানসিকতা আসলে শিল্পের মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি কৃত্রিম প্রাচীর তৈরি করে এবং শরীরকে জ্ঞানের জগৎ থেকে নির্বাসিত করতে চায়। এটি একধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বর্ণবাদ, যেখানে মানসিক শ্রমকে শারীরিক শ্রমের চেয়ে কৌলীন্যপূর্ণ মনে করা হয় এবং শরীরকে কেবলই নিয়ন্ত্রণের বস্তু হিসেবে দেখা হয়।
অর্থের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাখ্যার একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of Interpretation)
দ্বিতীয় বড় ভয়টি হলো অর্থের সরলীকরণ (Oversimplification)। বলা হয়, লালনের গান রূপক এবং ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। এর অর্থ বহুস্তরীয় এবং প্রায়শই রহস্যময়। নাচ, তার শারীরিক এবং দৃশ্যমান প্রকৃতির কারণে, এই বহুস্তরীয় অর্থকে একটি মাত্র আক্ষরিক (Literal) ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ করে ফেলে, যা গানের কাব্যিকতা এবং দার্শনিক গভীরতাকে হত্যা করে।
এই ভয়টি একদিক থেকে দেখলে সম্পূর্ণ অমূলক নয়। একটি দুর্বল বা বোধহীন কোরিওগ্রাফি নিঃসন্দেহে গানের অর্থকে খর্ব করতে পারে। “খাঁচার ভিতর অচিন পাখি” গানের সঙ্গে পাখির মতো ডানা ঝাপটানোর ভঙ্গি করাটা অবশ্যই এক ভয়ংকর সরলীকরণ। কিন্তু এই যুক্তিসঙ্গত ভয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে ব্যাখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার এক সূক্ষ্ম অথচ শক্তিশালী প্রবণতা।
যখন একটি গান কেবল শোনা হয়, তখন তার অর্থ শ্রোতার মনে ব্যক্তিগতভাবে তৈরি হয়। সেই অর্থের কোনো দৃশ্যমান, সর্বজনীন রূপ থাকে না। এটি একান্তে উপভোগের বিষয়। কিন্তু যখন একজন নৃত্যশিল্পী সেই গানকে তার শরীরের ভাষায় অনুবাদ করেন, তখন তিনি গানটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাকে (A Possible Interpretation) মূর্ত এবং দৃশ্যমান করে তোলেন। এই মূর্ত রূপটি বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, আলোচনার সুযোগ তৈরি করে, ভিন্নমতকে আমন্ত্রণ জানায়। শুদ্ধাচারীরা এই সম্ভাবনাকেই ভয় পান। তারা চান, গানের অর্থ কেবল তাদের নির্দেশিত পথেই ভাবা হোক। তারা চান, গানের একটিমাত্র ‘শুদ্ধ’ বা ‘অথেনটিক’ (Authentic) ব্যাখ্যা থাকবে, যা কেবল গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বা নির্দিষ্ট কিছু পণ্ডিতের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। রোলাঁ বার্ত (Roland Barthes) যাকে “লেখকের মৃত্যু” (The Death of the Author) বলেছেন, অর্থাৎ কোনো টেক্সটের অর্থ লেখকের উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে পাঠকের দ্বারা নির্মিত হয় – সেই ধারণাটি তাদের জন্য অস্বস্তিকর (Barthes, 1977)।
নাচ এই ব্যাখ্যার একনায়কতন্ত্রকে (Dictatorship of Interpretation) ভেঙে দেয়। এটি গানের অর্থকে উন্মুক্ত করে দেয়, বহু ব্যাখ্যার সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নেয়। একজন নৃত্যশিল্পী যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, তা-ই একমাত্র বা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা নয়। অন্য একজন শিল্পী সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে একই গানকে নাচতে পারেন। একজন দর্শক সেই নাচ দেখে নিজের মতো করে নতুন অর্থ তৈরি করতে পারেন। এই শৈল্পিক বহুত্ববাদ (Artistic Pluralism) রক্ষণশীল মননকে আঘাত করে, কারণ তারা চায় সবকিছু একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা থাকুক। তাই ‘সরলীকরণ’-এর দোহাই দিয়ে তারা আসলে নৃত্যের এই ব্যাখ্যামূলক শক্তিকেই অস্বীকার করতে চান। তারা চান না শিল্পের অর্থ গণতান্ত্রিক হোক; তারা চান অর্থের ওপর নিজেদের অভিভাবকত্ব বজায় রাখতে।
সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতার নামে স্থবিরতার রাজনীতি
তৃতীয় যুক্তিটি হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বিশুদ্ধতা (Purity) রক্ষার। বলা হয়, বাউল ঐতিহ্যে মঞ্চে পরিকল্পিত নাচ (Choreographed Dance) করার প্রচলন নেই, তাই এটি একটি বহিরাগত সংযোজন যা মূল সংস্কৃতিকে ‘দূষিত’ (Contaminate) করবে। এই ‘বিশুদ্ধতা’র ধারণাটি অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম (Eric Hobsbawm) যেমন দেখিয়েছেন, আমরা যাকে প্রাচীন ও অপরিবর্তনীয় ‘ঐতিহ্য’ বলে মনে করি, তার অনেক কিছুই আসলে অপেক্ষাকৃত নতুন এবং নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রয়োজনে ‘উদ্ভাবিত’ (Invented Tradition) (Hobsbawm & Ranger, 1983)।
পৃথিবীতে কোনো সংস্কৃতিই এক জায়গায় স্থির থেকে ‘বিশুদ্ধ’ অবস্থায় টিকে থাকেনি। প্রতিটি জীবন্ত সংস্কৃতিই একটি প্রবহমান নদীর মতো, যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির উপাদান গ্রহণ করে, নিজেকে পরিবর্তন করে এবং নতুন রূপ ধারণ করে। যে সংস্কৃতি নিজেকে পরিবর্তনের ভয়ে গুটিয়ে রাখে, তা জীবন্ত থাকে না, জাদুঘরের সম্পদে পরিণত হয়।
এই ‘সাংস্কৃতিক বিশুদ্ধতা’র ধারণাটি প্রায়শই রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী বা মৌলবাদী মতাদর্শের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তারা একটি কাল্পনিক ‘স্বর্ণযুগ’-এর কথা বলে এবং সেই যুগের ‘শুদ্ধ’ সংস্কৃতির নামে সব ধরনের পরিবর্তন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আধুনিকতার বিরোধিতা করে। লালনের ক্ষেত্রেও এই যুক্তিটি ব্যবহার করে তাকে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডির মধ্যে আটকে ফেলার চেষ্টা করা হয়। বলা হয়, লালন ‘আমাদের’ মাটির জিনিস, তাকে পশ্চিমা বা আধুনিক কোনো কিছুর সঙ্গে মেশানো যাবে না।
এটি একধরনের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতাবাদ (Cultural Isolationism), যা লালনের বিশ্বজনীন আবেদনকেই অস্বীকার করে। লালন যদি কেবল কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহলে আজ সারা বিশ্বে তাকে নিয়ে এত গবেষণা বা আগ্রহ তৈরি হতো না। তার দর্শন কাল ও স্থান (Time and Space) অতিক্রম করতে পেরেছে বলেই তিনি প্রাসঙ্গিক। সেই প্রাসঙ্গিকতাকে নতুন যুগের নতুন শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করলে তা দূষিত হয় না, বরং আরও সমৃদ্ধ হয়। ‘বিশুদ্ধতা’র নামে এই প্রতিরোধ আসলে পরিবর্তনের প্রতি এক গভীর ভীতি এবং সাংস্কৃতিক স্থবিরতাকে (Cultural Stagnation) টিকিয়ে রাখার এক রাজনৈতিক কৌশল।
এই তিনটি আপত্তির সম্মিলিত ফলাফল হলো শিল্পের ওপর একধরনের অভিভাবকত্ব (Paternalism) আরোপ করা। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, সাধারণ দর্শক বা শিল্পীরা লালনকে ‘সঠিকভাবে’ বোঝার ক্ষমতা রাখেন না, তাই তাদের জন্য একটি গাইডলাইন বা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজন। এই অভিভাবকত্বের মনোভাব শিল্পের গণতান্ত্রিক চরিত্রকে অস্বীকার করে এবং শিল্পকে মুষ্টিমেয় কিছু ‘বোদ্ধা’র ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে। এটি লালনের নিজের দর্শনেরই পরিপন্থী, যিনি কোনো প্রতিষ্ঠান বা শাস্ত্রের মাধ্যমে নয়, বরং নিজের দেহ ও মনের অনুসন্ধানের মাধ্যমেই সত্যকে জানতে বলেছিলেন।