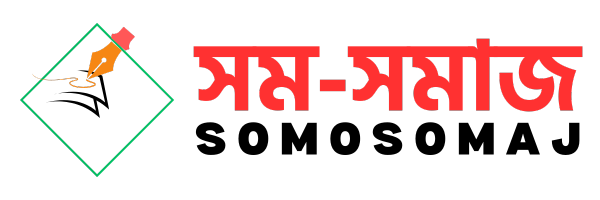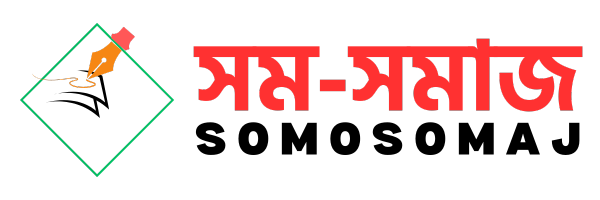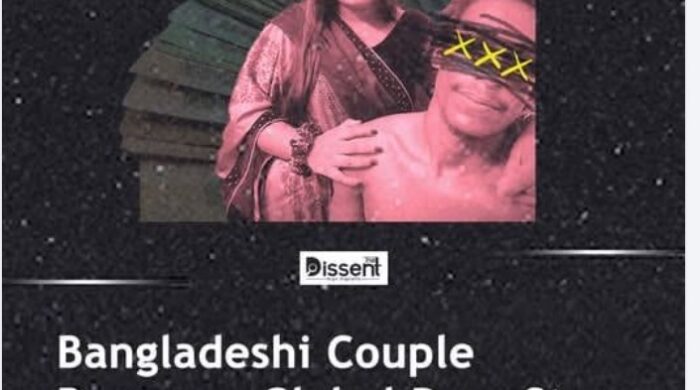অন্ধকার ঘরে জ্বলে থাকা মোবাইল ফোনের স্ক্রিনটা এখন আর শুধু বিনোদনের জানালা নয়, এটা এক নতুন পৃথিবীর দরজা। সেই পৃথিবীতে বাস্তবতা আর কল্পনার সীমারেখাগুলো বড্ড ঝাপসা। চট্টগ্রাম বা মানিকগঞ্জের মতো আটপৌরে কোনো অঞ্চলের সাধারণ এক তরুণ-তরুণী যে এই দরজার ওপাশে নিজেদের জন্য এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারে, তা হয়তো বছর দশেক আগেও ভাবা যেত না। তাদের গল্পটা কোনো ফিসফাস বা কানাঘুষার বিষয় নয়; এটি লক্ষ লক্ষ ভিউ আর ডলারের এক ঝলমলে উপাখ্যান। তারা নিজেদের শরীর ও জীবনকে এক পণ্যে পরিণত করেছে, যা বিক্রি হচ্ছে বিশ্বজুড়ে। এই ঘটনাকে কেবল নৈতিকতার দাঁড়িপাল্লায় মাপলে এর গভীরতা বোঝা যাবে না। এর পেছনে কাজ করছে এক জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক রসায়ন।
যখন কোনো জীবনযাপন নিছক বেঁচে থাকা থেকে সরে এসে প্রদর্শনীতে পরিণত হয়, তখন বুঝতে হবে আমরা এক ভিন্ন সময়ে প্রবেশ করেছি। এই তরুণ-তরুণী কেবল যৌনকর্মের ভিডিও তৈরি করছে না, তারা তাদের পুরো জীবনকেই একটি আকর্ষণীয় প্যাকেজ হিসেবে উপস্থাপন করছে। দামী মোটরবাইক, গাড়ির শোরুমে তোলা ছবি, আর টাকার বান্ডিলের ঝকঝকে প্রদর্শনী – এই সবকিছু তাদের কনটেন্টের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ফরাসি তাত্ত্বিক গি দ্যবোর (Guy Debord) এই পরিস্থিতিকে বলতেন “দৃশ্যপটের সমাজ” (Society of the Spectacle)। দ্যবোরের মতে, আধুনিক পুঁজিবাদী সমাজে আমাদের আসল অভিজ্ঞতা বা সম্পর্কগুলো হারিয়ে যায়, তার জায়গা নেয় নানা রকম চিত্র আর প্রতিচ্ছবি। আমরা আর বাস্তবকে ভোগ করি না, আমরা ভোগ করি বাস্তবের প্রতিরূপকে। এই দম্পতির জীবন সেই তত্ত্বের এক জীবন্ত উদাহরণ। তাদের সামাজিক মাধ্যমে অনুসারীরা কেবল তাদের যৌন ভিডিওর দর্শক নয়, তারা সেই জীবনেরও দর্শক, যা অর্থ, স্বাধীনতা আর বেপরোয়া মনোভাবের এক দারুণ মিশ্রণ। যেখানে তাদের গ্রামের প্রতিবেশীরা তাদের ‘অন্ধকার জগতের মানুষ’ বলে চিহ্নিত করছে, সেখানে ডিজিটাল পৃথিবীতে হাজার হাজার তরুণ তাদের দেখে ভাবছে – ‘জীবন তো এমনই হওয়া উচিত!’ এই দৃশ্যপট এতটাই শক্তিশালী যে, এর পেছনের কষ্ট বা অনুশোচনার গল্পগুলো – যেমন মেয়েটির ফেসবুক পোস্ট, “আমার জীবনের গল্প শুনলে যেকোনো মেয়ে কাঁদবে” – দর্শকদের চোখ এড়িয়ে যায়। কারণ দৃশ্যপটে কান্নার কোনো স্থান নেই, সেখানে কেবলই উদযাপনের ঝলকানি।
এই দৃশ্যপট তৈরির পেছনে যে বিশাল অর্থনৈতিক কাঠামো কাজ করছে, তাকেও হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই। ছেলেটি যখন টেলিগ্রামে তার আয়ের স্ক্রিনশট দিয়ে লেখে “মানি পাওয়ার”, তখন সে আসলে এক নতুন অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথাই ঘোষণা করে। এই ব্যবস্থাকে বুঝতে আমাদের তাকাতে হবে “প্ল্যাটফর্ম পুঁজিবাদ” (Platform Capitalism)-এর ধারণার দিকে। নিক স্রনিচেকের (Nick Srnicek) মতো তাত্ত্বিকরা দেখিয়েছেন, আজকের যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কোম্পানিগুলো কোনো পণ্য তৈরি করে না, তারা একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে। উবার যেমন কোনো গাড়ির মালিক নয়, কিংবা এয়ারবিএনবি যেমন কোনো হোটেলের মালিক নয়, তেমনি পর্নহাব বা অন্যান্য অ্যাডাল্ট সাইটগুলোও কোনো ভিডিও তৈরি করে না। তারা কেবল একটি ডিজিটাল পরিকাঠামো বা মঞ্চ তৈরি করে দেয়, যেখানে এই বাংলাদেশি দম্পতির মতো হাজারো কনটেন্ট ক্রিয়েটর নিজেদের শ্রম ও পণ্য নিয়ে হাজির হয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলো নির্মাতাদের একধরনের স্বাধীন ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তার অনুভূতি দেয়, কিন্তু আদতে তারা এই ডিজিটাল অর্থনীতির শ্রমিক। তাদের আয়ের প্রতিটি ডলারের একটি অংশ প্ল্যাটফর্মের মালিকদের পকেটে যায়। শুধু তাই নয়, নতুন ‘মডেল’ বা কর্মী নিয়োগের জন্য রেফারেল বোনাসের যে ব্যবস্থা, তা এই দম্পতিকে কেবল শ্রমিক থেকে একধাপ এগিয়ে প্ল্যাটফর্মের নিয়োগকর্তার ভূমিকাতেও বসিয়ে দিয়েছে। তারা যখন অন্যদের ‘ইনবক্স’ করতে বলে অর্থ উপার্জনের পথ দেখায়, তখন তারা আসলে এই ডিজিটাল পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই প্রসারে সাহায্য করে। তাদের দেখানো অর্থের লোভ তরুণদের সেই পথে টানছে, যেখানে শ্রমের সংজ্ঞা বদলে গেছে আর শরীরই হয়ে উঠেছে পুঁজি।
তবে এই গল্পের সবচেয়ে জটিল দিকটি হলো সমাজ ও ব্যক্তির সংঘাত। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী যা অপরাধ এবং সামাজিকভাবে যা লজ্জার বিষয়, সেটিই এই দম্পতির আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও আয়ের উৎস। এই দ্বন্দ্বটি আমাদের সমাজবিজ্ঞানের একটি পুরনো কিন্তু জরুরি বিতর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। হাওয়ার্ড বেকারের (Howard S. Becker) মতো তাত্ত্বিকরা “বিচ্যুতি” (Deviance) বা সামাজিক অবাধ্যতার ধারণাকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মতে, কোনো কাজ নিজে থেকে ভালো বা মন্দ নয়। সমাজই কিছু নিয়ম তৈরি করে এবং যারা সেই নিয়ম ভাঙে, তাদের গায়ে ‘বিচ্যুত’ বা ‘অপরাধী’ তকমা লাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ, বিচ্যুতি কোনো ব্যক্তির কাজের মধ্যে থাকে না, বরং সমাজের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থাকে। এই দম্পতি ঠিক এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। তাদের বাবা যখন বলেন, “আমি তাকে ত্যাগ করেছি”, কিংবা গ্রামের মানুষ যখন তাদের পরিবারকে ‘অপরাধী’ বলে চিহ্নিত করে, তখন সমাজ তার নিয়ম প্রয়োগ করে তাদের ‘বহিরাগত’ বা ‘আউটসাইডার’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ডিজিটাল বিশ্বে এই ‘বহিরাগত’ পরিচয়টাই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। যে পরিচয়ের কারণে তারা নিজ গ্রামে অস্পৃশ্য, সেই পরিচয়ের কারণেই তারা বিশ্বজুড়ে পরিচিত। তারা সমাজের দেওয়া এই তকমাকে লজ্জা হিসেবে না নিয়ে, বরং একটি ব্র্যান্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের এই উত্থান প্রমাণ করে, এক সমাজে যা বিচ্যুতি, অন্য এক ডিজিটাল বা বৈশ্বিক সমাজে তা-ই হয়ে উঠতে পারে গ্রহণযোগ্যতা বা এমনকি খ্যাতির কারণ।
শেষ পর্যন্ত, এই গল্প কেবল দুই ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার গল্প নয়। এটি আমাদের সময়ের গল্প। যেখানে একটি স্মার্টফোনের স্ক্রিন একই সাথে কাউকে তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, আবার তাকেই জুড়ে দেয় এক অচেনা বিশ্বের সাথে। যেখানে অর্থ আর খ্যাতির দৃশ্যপট এতটাই মোহময় যে এর আকর্ষণে তরুণেরা নির্দ্বিধায় ঝাঁপ দিতে চায়। এই নতুন কারিগররা যে দৃশ্যপট তৈরি করছে, তার আলো হয়তো অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু সেই আলোর নিচে যে গভীর অন্ধকার লুকিয়ে আছে, তার খবর হয়তো আমরা কোনোদিনই পাবো না।