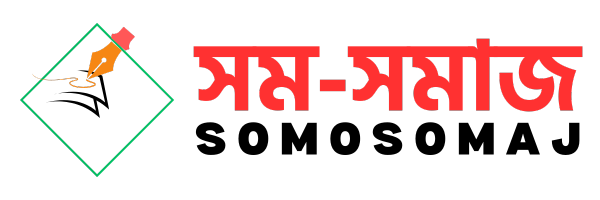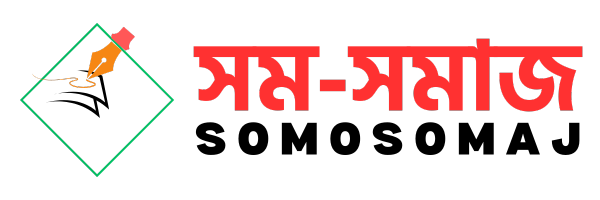ছয় মাস আগেও যা কেউ কল্পনা করতে পারেনি, সেটাই সত্যি হলো। জোহারান মামদানি নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে জিতে গেলেন। মামদানির এই উল্কার মতো উত্থান (meteoric rise) কেবল আমেরিকার ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকেই নয়, বরং সারা বিশ্বের ধুঁকতে থাকা বামপন্থী দলগুলোর মধ্যেও তুমুল আগ্রহের জন্ম দিয়েছে। সবাই এখন অবাক হয়ে ভাবছে, এই আকস্মিক ও অভাবনীয় সাফল্য থেকে তারা কী শিখতে পারে? মামদানি নিজেকে ট্রাম্পের ‘সবচেয়ে বড় দুঃস্বপ্ন’ বলে পরিচয় দেন, যদিও ট্রাম্প তাকে ‘একশ ভাগ কমিউনিস্ট উন্মাদ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আজকের এই লেখায় আমরা দেখব, এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় ডেমোক্র্যাটিক পার্টি তার কাছ থেকে কী পাঠ নিতে পারে।
শুরুতেই একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। আমেরিকার সবচেয়ে উদারপন্থী (liberal) শহরগুলোর একটিতে, একটি সাধারণ বছরে অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচন থেকে জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি সিদ্ধান্তে আসাটা হয়তো ঠিক না। বিশেষ করে যখন বিরোধী পক্ষে ছিলেন অ্যান্ড্রু কুওমো আর কার্টিস স্লিওয়ার মতো প্রার্থীরা। তাছাড়া, আগামী কয়েক বছরে মামদানি কতটা সফল হন বা ব্যর্থ হন, তার ওপরই নির্ভর করবে ডেমোক্র্যাটরা তার অভিজ্ঞতা থেকে ঠিক কী শিখবে। যদি তিনি সফল হন এবং জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে পারেন, তবে তিনি হয়তো ডেমোক্র্যাটদের নতুন প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন। আর যদি ব্যর্থ হন, তবে তাকে একটি সতর্কতামূলক উদাহরণ হিসেবেই তুলে ধরা হবে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো মাথায় রেখেও, আমরা মামদানির সাম্প্রতিক সাফল্য থেকে অন্তত চারটি আপাত (tentative) শিক্ষা খুঁজে নিতে পারি। ‘সোশ্যাল মিডিয়াতে আরও দক্ষ হতে হবে’ বা ‘প্রতিষ্ঠানের মতো আচরণ করা যাবে না’ – এইসব গতানুগতিক পরামর্শের বাইরে গিয়ে গভীরে তাকানোর চেষ্টা করা যাক।
জীবনের যাঁতাকল ও সাধারণ মানুষের ভোটের লড়াই
ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরে এখন একটা বড় বিতর্ক চলছে। তাদের কি ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার গণতন্ত্রের (democracy) জন্য যে হুমকি তৈরি করেছেন, সেটার ওপর বেশি জোর দেওয়া উচিত? নাকি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সংগ্রাম, যেমন – ডিমের দাম বাড়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা উচিত? প্রথম পথের সমর্থকরা বলেন, যখন ট্রাম্প আমেরিকান গণতন্ত্রের কাঠামোই ছিঁড়ে ফেলছেন, তখন মানুষের জীবনযাত্রার খরচ নিয়ে কথা বলাটা খুব তুচ্ছ শোনায়। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পথের প্রবক্তারা বলেন, ভোটাররা আসলে তাদের ডাল-ভাতের চিন্তা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। মূল্যস্ফীতির (inflation) মতো বিষয়গুলো তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পরিসংখ্যানও দ্বিতীয় দলটির কথাই বলছে। নেট সিলভারের পোলিং অ্যাগ্রিগেটর (polling aggregator) অনুযায়ী, মূল্যস্ফীতির প্রশ্নে ট্রাম্পের অবস্থা সবচেয়ে দুর্বল। এই ইস্যুতে তার নেট অনুমোদন রেটিং (net approval rating) বর্তমানে মাইনাস ৩০, যা তার ব্যক্তিগত রেটিংয়ের চেয়েও প্রায় ২০ পয়েন্ট কম (Silver, n.d.)। এছাড়া, অনেকেই মনে করেন, গণতন্ত্রের ওপর ট্রাম্পের আক্রমণ নিয়ে বেশি কথা বললে ডেমোক্র্যাটদের স্থিতাবস্থার (status quo) রক্ষক বলে মনে হয়, যা বর্তমান রাজনৈতিক আবহে খুব একটা আকর্ষণীয় কৌশল নয়। অবশ্যই, এই দুটি পথ পরস্পরবিরোধী নয়। ডেমোক্র্যাটরা চাইলে দুটো অস্ত্রই ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, তা নিয়ে দলে বিতর্ক আছে। মামদানির সাফল্য প্রমাণ করে যে, মানুষের জীবনযাত্রার খরচকে প্রাধান্য দেওয়াটাই সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ। মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার মূল ভিত্তিই ছিল জীবনযাত্রার খরচ কমানোর প্রতিশ্রুতি। যদিও তথাকথিত সংস্কৃতি যুদ্ধের (culture war) মতো বিষয়গুলোতে তিনি অবস্থান নিতে ভয় পাননি, কিন্তু সেগুলো তার প্রচারণার কেন্দ্রে ছিল না। বিশেষ করে, মামদানি আবাসন ব্যবস্থার আকাশছোঁয়া খরচ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন। তার নীতিগুলো বাস্তবে কাজ করবে কিনা, তা নিয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ সন্দিহান থাকলেও, ভোটাররা যে এই বিষয়ে তার মনোযোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে, তা স্পষ্ট।
এই অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিকভাবেও সত্যি। যেমন, নেদারল্যান্ডসে লিবারেল ডি৬৬ (Liberal D66) পার্টি গির্ট ওয়াইল্ডারের পিভিভি-র (PVV) বিরুদ্ধে আশ্চর্যজনক জয় পেয়েছিল। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাদের প্রচারণার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল নেদারল্যান্ডসের আবাসন সংকট সমাধান করা (Cox, 2021)। আমরা হয়তো ভুলে গেছি, কমলা হ্যারিসের প্রচারণার শুরুর দিকে এমন একটা সময় ছিল যখন তিনি প্রথমবারের মতো বাড়ি ক্রেতাদের জন্য ২৫,০০০ ডলারের ট্যাক্স ক্রেডিটের (tax credit) প্রস্তাবকে খুব গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবটি জরিপে বেশ ভালো সাড়া ফেলেছিল এবং প্রচারণার প্রথম দিকে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে তাকে সাহায্যও করেছিল (YouGov, n.d.)।
রাজনীতির উঠোনে একচিলতে ইতিবাচকতার হাসি
মামদানির নির্বাচনী প্রচারণা ছিল নিঃসন্দেহে ইতিবাচক (positive)। তিনি ছিলেন অক্লান্তভাবে আশাবাদী, মুখে সবসময় হাসি লেগেই থাকত – হয়তো প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই। যারা তার সঙ্গে একমত হতেন না, তাদের সঙ্গেও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার চেষ্টা করতেন। যেমন, ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারির সময় ব্র্যাড ল্যান্ডারের সঙ্গে ইসরায়েল ইস্যুতে তীব্র মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ নির্বাচনী জোট (amiable electoral alliance) গঠন করেছিলেন। মামদানি মনে করেন, ইসরায়েলের একটি ইহুদি রাষ্ট্র হওয়া উচিত নয়, অন্যদিকে ল্যান্ডার নিজেকে একজন উদার জায়নবাদী (liberal Zionist) হিসেবে পরিচয় দেন এবং মামদানির মতো ‘গ্লোবালাইজ দ্য ইন্তিফাদা’ – এই শব্দগুচ্ছের দ্ব্যর্থহীন নিন্দা করেছেন।
এ কারণেই মামদানিকে যখন গণমাধ্যম ‘পপুলিস্ট’ (populist) বা জনতোষণবাদী বলে, তখন ব্যাপারটা ঠিক মেলে না। পপুলিস্টরা সাধারণত বেশ নেতিবাচক হন। তারা রাজনীতিকে ‘আমরা বনাম ওরা’ – এই বিভাজনের চোখে দেখেন এবং নিজেদের নির্বাচনী জোট থেকে নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীকে বাদ দিতে দ্বিধা করেন না।
আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাও বলে যে, রাজনীতিতে ইতিবাচকতা কাজ করে। যেমন, যুক্তরাজ্যে গ্রিন পার্টির (Green Party) সাম্প্রতিক উত্থানের পেছনে তাদের নতুন নেতা জ্যাক পোলানস্কির আশাবাদকে বড় করে দেখা হয়। পোলানস্কি ‘আশাকে আবার স্বাভাবিক করতে চান’ (make hope normal again)।
‘বামপন্থী’ তকমা কি এখন আর ভয়ের কিছু নয়?
কয়েক দশক ধরে ডেমোক্র্যাটরা ‘সমাজতন্ত্রী’ (socialist) তকমাকে ভয় পেয়ে এসেছে। যে দেশ নিজেকে পুঁজিবাদের (capitalism) দুর্গ হিসেবে দেখতে ভালোবাসে, সেখানে এই ভয়টা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু মামদানি নিজেকে একজন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী (democratic socialist) হিসেবে পরিচয় দেন। তিনি বলেছেন, তিনি বিলিয়নেয়ারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না এবং একাধিক বামপন্থী অর্থনৈতিক নীতিকে সমর্থন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে – কর্পোরেট ট্যাক্সের হার (corporate tax rate) বাড়ানো, বাস পরিষেবা বিনামূল্যে করে দেওয়া, ভাড়া বৃদ্ধি বন্ধ করা, সরকারি খরচে শিশু যত্ন কেন্দ্র তৈরি, এমনকি খাবারের দাম কমানোর জন্য কয়েকটি রাষ্ট্রীয় মুদি দোকান খোলার মতো প্রস্তাবও। আশ্চর্যজনকভাবে, এসবের কোনোটিই তার জন্য নির্বাচনী বিপর্যয় ডেকে আনেনি, যা একসময় ভাবা হতো। এর কারণ দুটো। প্রথমত, দীর্ঘস্থায়ী মূল্যস্ফীতি আমেরিকানদের সরকারি সমাধানের প্রতি আরও বেশি উন্মুক্ত করে তুলেছে। দ্বিতীয়ত, র্যাডিকাল বামপন্থী (radical left-wing) নীতি গ্রহণ করলে একজন প্রার্থীর প্রতিষ্ঠানবিরোধী (anti-establishment) পরিচয় আরও জোরালো হয়। আর এই মুহূর্তে ডেমোক্র্যাটদের সবচেয়ে বড় নির্বাচনী দুর্বলতা সম্ভবত তাদের প্রতিষ্ঠানপন্থী (pro-establishment) ভাবমূর্তি। সম্ভবত একারণেই বার্নি স্যান্ডার্স, একজন ঘোষিত সমাজতন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও, ধারাবাহিকভাবে কংগ্রেসের অন্যতম জনপ্রিয় নেতাদের একজন হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন।
নেতা কে হবেন, সেই ভাবনা নাহয় ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক
ডেমোক্র্যাটরা এখন তাদের নেতৃত্ব নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন, এবং এর কারণও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। দলের বেশিরভাগ সিনিয়র নেতাই এখন বেশ অজনপ্রিয়। ২০২৮ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর মতো কোনো স্পষ্ট রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী তাদের হাতে নেই। বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসমের (Gavin Newsom) নাম সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে। নিউসম নিঃসন্দেহে একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ এবং ২০২৮ সালে জেতার সম্ভাবনা তার আছে, কিন্তু তার পথ মোটেও মসৃণ নয়। রিপাবলিকানরা আশাবাদী যে, তারা তাকে ‘পশ্চিম উপকূলের বামপন্থী’ (West coast lefty) হিসেবে তুলে ধরতে পারবে, যার সঙ্গে সাধারণ আমেরিকানদের কোনো যোগাযোগ নেই।
মামদানির আকস্মিক উত্থান ডেমোক্র্যাটদের মনে করিয়ে দেয় যে, এত চিন্তার কিছু নেই। নতুন মুখের আবির্ভাবের জন্য এখনো অনেক সময় বাকি। ২০২৮ সালে তাদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী কে হবেন, তা ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রায় অসম্ভব। মামদানির দিকেই দেখুন। মাত্র কয়েক মাস আগেও তিনি ছিলেন কার্যত একজন অচেনা মুখ, আর এখন তিনি আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত একটি নাম।
ব্যাপারটা কিছুটা হলেও সবসময়ই এমন ছিল। যেমন, ২০০৫ সালে খুব কম মানুষই ভেবেছিল যে বারাক ওবামা, যিনি মাত্রই সিনেটর নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এটা আরও বেশি সত্যি হয়ে উঠেছে। মামদানির মতো ‘ভাইরাল’ (viral) হয়ে গেলে একজন রাজনীতিবিদের ভাগ্য রাতারাতি বদলে যেতে পারে। জোহারান মামদানি কোনো জাদুকর নন, কিন্তু তার সাফল্য হয়তো ডেমোক্র্যাটদের জন্য একটি নতুন পথের দিকে ইশারা করছে। সেই পথটি কেমন হবে, তা সময়ই বলে দেবে।