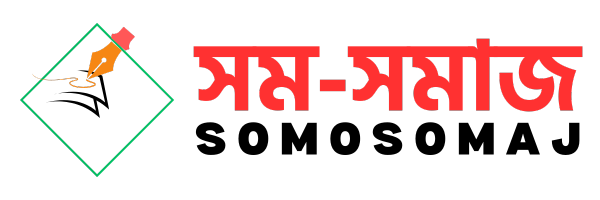
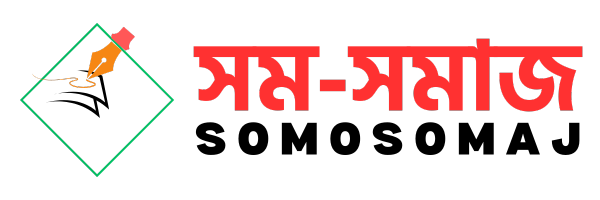
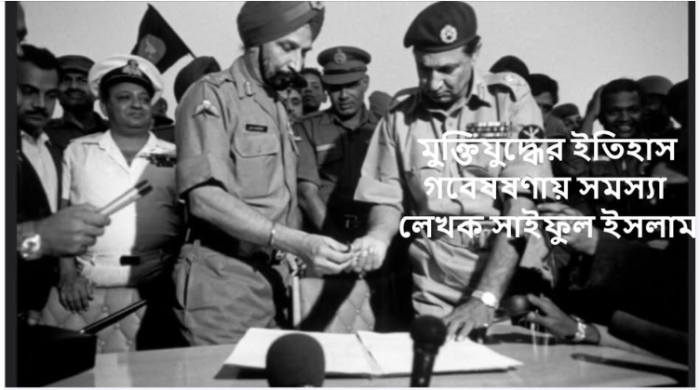
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়। এটি শুধু একটি স্বাধীনতার সংগ্রাম ছিল না, বরং এটি বাঙালির আত্মপরিচয় এবং জাতি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় লাখ লাখ বাঙালি নিজের জীবন উৎসর্গ করে একটি স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা এবং গবেষণার ক্ষেত্রে এখনও অনেক অন্ধকারে রয়ে গেছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্বাধীনতার পর থেকে যে ইতিহাস চর্চা হয়ে আসছে, তা অনেক ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ এবং একপেশে। বিশেষত, মুক্তিযুদ্ধের ছোট ছোট ঘটনা, স্থানীয় সংগ্রাম, এবং জনগণের ভূমিকা প্রায়শই উপেক্ষিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে প্রধানত কেন্দ্রীয় রাজনীতি, বড় যুদ্ধ, তারকা মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ, এবং নারীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনাগুলিই বেশি আলোচিত হয়। তবে, যুদ্ধের অন্যান্য দিক যেমন ছোট যুদ্ধ, গেরিলা সংগ্রাম, এবং বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা তেমন হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এতে মুক্তিযুদ্ধের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে আসেনি, বিশেষত যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায়, ছোট ছোট যুদ্ধের গুরুত্ব, এবং মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ ধারাবাহিক আন্দোলনের যে ভূমিকা ছিল তা অনেক সময় উপেক্ষিত হয়।
মুক্তিযুদ্ধের ধারণাপত্রে বলা হয়েছে এক রকম, সে অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সাজানোর প্রবণতা লক্ষণীয়। প্রস্তাবে যা আছে সে অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বাহিনী তাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করেছে কি-না, দায়িত্ব পালন করে না থাকলে কেন তা হয়নি- তারও যে গবেষণা প্রয়োজন সেদিকে গবেষকেরা যাচ্ছেন না। তাছাড়া এখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রধান তথ্যদাতা মুক্তিযোদ্ধা, কারণ তারাই যুদ্ধ করে স্বাধীনতা এনেছে। কিন্তু তারা কী জানে যে দেশের অভ্যন্তরে কী ঘটেছে? যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তারা কী খোঁজ নিয়েছে যে তার এমনকি নিজের গ্রামে কী কী ঘটনা ঘটেছে? তারাতো যে যে এলাকায় যেটুকু যুদ্ধ করেছে সেটুকুই জানে। তারা কী কখনো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা করেছে। সে হিসেবে তাদের স্মৃতি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাদের ওপর ইতিহাস চর্চায় কতটুকু নির্ভর করা যায় তা ভেবে দেখা দরকার। আসলে মূল তথ্য দাতা করা প্রয়োজন জনগণকে, যারা এলাকায় থেকে পাকসেনা ও স্বাধীনতা বিরোধীদের দাবড়ানি খেয়ে টিকে থাকার চেষ্টা করেছে।
১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত গণঅভ্যূত্থান পর্ব। ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশকে পূনর্দখলে নামে পাকসেনারা। এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রতিটি জেলা ও মহুকুমা সদর দখলে নেয় তারা। দখল শেষে গণঅভ্যূত্থানে এলোমেলো হয়ে যাওয়া প্রশাসন পূণর্গঠন করে পাকিস্তান সরকার। তাড়া খাওয়া আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের প্রধান অংশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর, পুলিশ, আনসার সদস্যরা চলে যায় সীমান্তের ওপারে। এ সময় কেউ কেউ আত্মগোপন করে দেশের ভিতরেই থেকে যায় বা থাকতে বাধ্য হয়। এদের নেতৃত্বে গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা গ্রæপ। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এই গ্রæপগুলো নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পাক সশস্ত্র বাহিনীর বিদ্রোহী সদস্যদের ওপর। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে এই গ্রæপগুলো পরিচালিত হতে থাকে তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা অনুযায়ী পাকিস্তানি নিয়মিত বাহিনীর আদলে। গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় গেরিলা গ্রæপের পরিবর্তে এরা হয়ে উঠতে থাকে স্থানীয় বাহিনী, অনেকটা ভ্রাম্যমান নিয়মিত বাহিনীর মতো। টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জের পলাশডাঙ্গা যুব শিবির, পাবনার বকুল-ইকবাল গ্ৰুপ , কুষ্টিয়ার হাদী গ্ৰুপ , যশোরের বিএলএফ গ্ৰুপ , খুলনার কামরুজ্জামান গ্ৰুপ , মাগুরার আকবর বাহিনী, মাদারীপুরের শাহজাহান গ্ৰুপ হয়ে ওঠে এক একটি ভ্রাম্যমান নিয়মিত বাহিনী।
ভারতের সহযোগিতায় ও নানা ধারায় সংঘটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। যেমন- মুক্তিফৌজ, এফএফ, বিএলএফ বা মুজিব বাহিনী – এদের বিষয়ে যা বলা হয় তার প্রতিফলন কি যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে? পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহী বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যদের নিয়ে গঠণ করা হয় মুক্তিফৌজ। সবাই কিন্তু সে বিদ্রোহে অংশ নেয়নি। প্রয়োজনের তূলনায় সংখ্যা কম হওয়ায় এদের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ইপিআর, পুলিশ, আনসার এমনকি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদেরও। এই মুক্তিফৌজের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। প্রবাসী সরকারের কাছে থেকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পায় এই মুক্তিফৌজ। প্রধান সেনাপতি, সেক্টর কমান্ডার, সাব-সেক্টর কমান্ডারও নিযুক্ত হন মুক্তিফৌজ থেকে। মুক্তিফৌজের এ কর্মকর্তারা মূলত প্রথাগত যুদ্ধের ধারণা নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে আসে এবং সে কৌশলেই মুক্তিযুদ্ধের উদ্যোগ নেয়। মুক্তিফৌজ মনে করতো, নিয়মিত বাহিনীকে শক্তিশালী করে একসময় দখলমুক্ত করা হবে বাংলাদেশ। সে হিসেবেই জেড ফোর্স, কে ফোর্স এস ফোর্স গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কুড়িগ্রামের রৌমারী এলাকায় মুক্তিফৌজের স্থায়ী প্রশিক্ষণ ক্যাম্প এবং সেনানিবাস গঠনের চিন্তাও করা হয়। এরা সীমান্ত এলাকায় প্রধানত ভারতের মাটিতে ঘাঁটি করে বাংলাদেশের পনের মাইল অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর ওপর হামলা পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর এদের নিয়ে গঠন করা হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী গঠনের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নিয়ে গঠন করা হয় যৌথ বাহিনী। ১১ টি সেক্টরের পরিবর্তে গঠন করা হয় ৪টি সেক্টর। অবশেষে মিত্র বাহিনীর সহায়তায় মুক্ত হয় বাংলাদেশ।
এফএফ মুক্তিযোদ্ধারা প্রবাসী সরকার সৃষ্ট গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। প্রবাসী সরকার এদের নাম রাখে ‘গণবাহিনী’। ভারতীয় সেনাবাহিনী এফএফকে প্রশিক্ষণ দিতো চার সপ্তাহ পরে তিন সপ্তাহ করে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ এদের দেশের ভিতরে পাঠানোর সময় বলতেন, ‘আমরা তোমাদের প্রশিক্ষণ দিতে পারিনি, শুধু অস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যুদ্ধ শিখবে যুদ্ধক্ষেত্রে, যুদ্ধ করতে করতে।’ এই গেরিলা যোদ্ধাদের কোথায় যুদ্ধ করার কথা? অবশ্যই তাদের নিজের পরিচিত এলাকায় পরিচিত জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবে। কারণ গেরিলা যুদ্ধের প্রধান মন্ত্রই ‘জনগণ হচ্ছে পানি, আর গেরিলারা হচ্ছে সেই পানিতে বিচরণকারী মাছ।’ কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেছে কি? জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এফএফ প্রথম ব্যচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়। অস্ত্র সরবরাহ সহ নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে এফএফ মুক্তিযোদ্ধারা জুলাই মাসে যুদ্ধক্ষেত্রে আসার সুযোগ পায়। কিন্তু কোন যুদ্ধক্ষেত্র? এফএফ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রথমে এদের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তযুদ্ধে নিয়োজিত করা হয়। সেখানে তাদের মুক্তিফৌজ বা বিএসএফের অধীনে ‘ডিফেন্সে’ যুদ্ধ করে ‘সাহস’ অর্জন করতে বলা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ছয় ব্যচে প্রায় ৭৫,০০০ এফএফ মুক্তিযোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, এফএফ মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল অংশ নিজের পরিচিত এলাকায় পা-ই রাখতে পারেনি।
আসা যাক বিএলএফ প্রসঙ্গে, যারা নিজেদের পরিচিত করে ‘মুজিব বাহিনী’ হিসেবে। প্রবাসী সরকারের অজ্ঞাতে ভারতীয় বাহিনীর দ্বারা প্রশিক্ষণ পায় এরা। ্প্রবাসী সরাকারের একটি ক্ষোভও রয়েছে যে তাদের না জানিয়ে বিএলএফ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের ভিতরে পাঠানো হয়। আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কর্মীদের নিয়ে গঠিত মুক্তিযোদ্ধাদের ধারা এটি। বিএলএফ নেতারা বলেন, জনগণের পাশাপাশি যদি মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান না থাকে, তাবে জনগণ হতাশ হয়ে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে, তাই দেশের ভিতরে যুদ্ধ করার জন্য এ বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এ বাহিনী সীমান্ত এলাকার ১৫ মাইল পর্যন্ত যুদ্ধ করার সুযোগ পেতো না। সিরাজুল আলম খানের দাবি অনুযায়ী ভারতে প্রশিক্ষিত বিএলএফ সদস্য প্রায় ৮ হাজার। দেশের ভিতরে এসে গ্রাম কমিটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করে তাদের অধীনে ছোট ছোট গেরিলা গ্রæপ গড়ে তোলার কথা ছিল এদের। কিন্তু গ্রাম কমিটি ইউনিয়ন কমিটি এবং তার অধীনে ছোট ছোট গেরিলা গ্ৰুপ গড়ে তোলার পরিবর্তে তারাও গড়ে তোলে স্থানীয় বাহিনী। এভাবেই গড়ে ওঠে সিরাজগঞ্জে লতিফ মির্জা বাহিনী (পলাশডাঙ্গা যুব শিবির), পাবনায় বকুল-ইকবাল গ্ৰুপ , কুষ্ঠিয়ায় হাদী ও অন্যান্য গ্ৰুপ , যশোরের রবিউল ইসলাম, খুলনার কামরুজ্জামান টুকু, মাদারীপুরের শাজাহান খানসহ প্রতিটি জেলায় বিএলএফের একাধিক বাহিনী। বিভিন্ন জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ঘাঁটলে দেখা যায়, বিএলএফ থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের যে রাজনৈতিক কৌশলে যুদ্ধ করার কথা, তা না করে প্রথাগত যুদ্ধকৌশলে অংশ নেন এ মুক্তিযোদ্ধারা। ফলে তাদের যুদ্ধ বিএলএফের যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিএলএফের রাজনীতি, যুদ্ধ কৌশল এবং তার প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা হওয়া খুবই জরুরী। ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে অস্ত্র জমা দেওয়ার সময় জানা যায় যে, ভারতে মাত্র ৮ হাজার মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ নিলেও ভিতরে রিক্রুটসহ এদের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৭০ হাজার।
বিএলএফ সম্পর্কে দুটি অভিযোগ তোলা হয়। এক. এরা ‘বামপন্থী’দের নিধনের জন্য ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এ বাহিনী প্রতিষ্ঠিত; দুই, এরা কোনও যুদ্ধে অংশ নেয়নি। কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, ২৫ মার্চের আগের ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্ৰুপের বিরোধের জের ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোথাও কোথাও ‘বামপন্থী’দের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তা সর্বত্র নয়। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে পাবনা সদর মহুকুমার। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে নক্সালপন্থীরা হত্যা করে তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা ১৯৭০ সালে নির্বাচনে নির্বাচিত এমপিএ আহমেদ রফিককে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা হত্যার দাবি করেছেন তৎকালীন নকশাল নেতা টিপু বিশ্বাস। [ পৃষ্ঠা -৩৮১, মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী – লেখক আলতাফ পারভেজ ] যার জের চলে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়কাল জুড়ে, এমনকি পরবর্তীতেও। কিন্তু পাশ্ববর্তী সিরাজগঞ্জে তা ঘটেনি। সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার মোহনপুর ইউনিয়নের এলংজানিতে ‘বামপন্থী’ কয়েকজন কর্মীকে হত্যা করা হয়, কিন্তু এ ঘটনা ঘটে পাবনা থেকে আগত মুক্তিবাহিনীর বাহিনীর দ্বারা। আবার অনেক স্থানেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘটনাও পাওয়া যায়, যেমন চাঁদপুর, কুমিল্লা, হবিগঞ্জে। কুমিল্লা এফএফ গ্ৰুপের অন্যতম নেতা ছিলেন বর্তমান বাসদ নেতা খালেকুজ্জামন। তিনি আবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট গ্ৰুপের সাথে যুক্ত ছিলেন। হবিগঞ্জের জগৎজ্যোতি দাস ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্ৰুপের কর্মী। তাই ঢালাও এ মূল্যায়ন সন্তোষজনক নয়। দুই নম্বর অভিযোগও ব্যাপক গবেষণার দাবি করে।
খোদ প্রবাসী সরকার সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যায় যে এর মূল নেতা কে ছিলেন? তাজউদ্দিন নাকি সৈয়দ নজরুল ইসলাম? ‘১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নির্বাচিত পরিষদ সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রচারিত স্বাধীনতা আদেশ ঘোষণায় শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের গণপ্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয় এবং এই আদেশটি ২৬ মার্চ থেকে কার্যকারিতা লাভ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়।’ (মূলধারা ’৭১। মঈদুল হাসান। পৃষ্টাÑ ১৬। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। ত্রয়োদশ মুদ্রণ এপ্রিল ২০১৭।) এটি মুজিবনগর সরকারের ঘোষণা হিসেবে জনগণের কাছে পরিচিত। এ ঘোষনা অনুযায়ী মুজিবনগর সরকারের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকার সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু আমরা বাস্তবে দেখতে পাই সকল ক্ষমতার অধিকারী তাজউদ্দিন আহমদ। সকল আলোচনা সমালোচনা, প্রসংশা-নিন্দার অধিকারী হন তিনি। এবিষয়ে গবেষকদের দৃষ্টি দেওয়া জরুরী যে মুজিবনগর সরকারের ঘোষণার ব্যত্যয় কেন কিভাবে ঘটেছে? এটা কী ভারত সরকারের অনীহা নাকি সৈয়দ নজরুল ইসলামের অদক্ষতা?
মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থীদের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা ছিল। চীন পন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ৫/৬ ভাগে বিভক্ত ছিল। অঞ্চল ভেদে এই সমস্ত গ্ৰুপের কোন কোন অংশের নেতৃত্বে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে উঠেছিল। তবে এই সব প্রতিরোধ যুদ্ধের মধ্যে কোন পারস্পরিক যোগাযোগ ছিল না। বিভিন্ন গ্রূপ বিভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে যুদ্ধ করেছে। শিবপুর নরসিংদীর প্রতিরোধ যুদ্ধের সাথে যশোর বা পেয়ারাবাগানের কৌশলগত কোন ঐক্যমত বা যোগাযোগের কথা জানা যায় না। যশোরে বিমল বিশ্বাসের নেতৃত্বে শুরুতে পাকিস্তানী বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছে। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল ) নামে রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছে। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উঠতে পারে বিমল বিশ্বাসরা কোন ভূখণ্ডের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ! স্বাধীনতার পর মোহাম্মদ তোয়াহা পূর্ব বাংলার সাম্যবাদী দল ( এম-এল ) নাম দিয়ে রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে এসে দলের নাম পূর্ব বাংলা থেকে বদলিয়ে বাংলাদেশ রাখেন। মুক্তিযুদ্ধে ‘বামপন্থী’ বিভিন্ন ধারা ক্রিয়াশীল দেখতে পাই, তারা তাদের ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করেছে। তাদের বিষয়ে আলোচনা না হলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।
মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের রাজনীতি এবং স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গবেষণাকে আরও জটিল করে তুলেছে। যুদ্ধের পর স্বাধীনতার পক্ষে যারা সংগ্রাম করেছে, তাদের তথ্য সংগ্রহে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রিক কিছু গবেষক কিছু প্রশ্নপত্র ছেড়ে দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা করার পদ্ধতি চেষ্টা করছেন। এই পদ্ধতি অ কার্যকর। কারণ প্রতিটি এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভিন্ন। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা, স্বাধীনতা বিরোধীদের উত্থান এবং তাদের প্রোপাগান্ডা মোকাবেলা করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তির একটি দৃঢ় আন্দোলন প্রয়োজন, যা জনগণকে সঠিক তথ্য দিয়ে গবেষকদের সাহসী পদক্ষেপ নিতে উদ্বুদ্ধ করবে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রকৃত চিত্র সবার সামনে তুলে ধরতে হলে, শুধু বড় যুদ্ধের ঘটনা নয়, বরং স্থানীয় যুদ্ধ, জনগণের সংগ্রাম, ছোট বাহিনীর ভূমিকা, এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটিত সংঘর্ষগুলোও আলোচনায় আসা উচিত। সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং বাঙালি জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়টি সঠিকভাবে চিহ্নিত হবে।
লেখক: মুক্তিযোদ্ধা, আহ্বায়ক সিরাজগঞ্জের গণহত্যা অনুসন্ধান কমিটি।