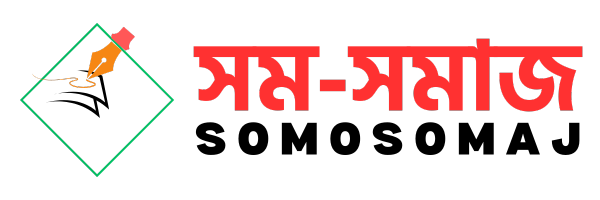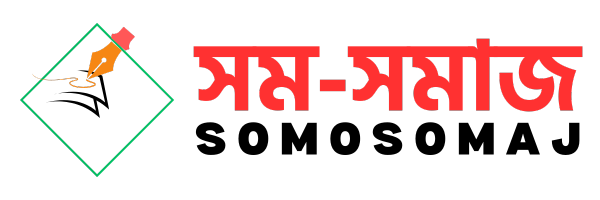সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাশে স্থাপিত একটি নারীমূর্তির উপর আক্রমণ ধর্মান্ধতা, লিঙ্গবিদ্বেষ এবং রাজনৈতিক ধর্মবাদের এক নির্মম প্রতিচ্ছবি। এই নারীমূর্তিটি ছিলো একটি নৈর্ব্যক্তিক চিত্র: কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি বা পরিচিত মুখ নয়, বরং একটি প্রতীকী নারী, যার মুখ কালো কাপড়ে আবৃত ছিলো। তবু সেটিকে বেছে নেওয়া হলো, বস্ত্রহরণ করা হলো, জুতোপেটা করা হলো—এ যেন আমাদের সমাজে নারীর প্রতীকীকেই প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করা।
এই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ নয়। বরং এটি একটি বৃহত্তর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের অংশ। নারী সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশের পর জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলাম এবং এনসিপি -এর নেতারা যে ধরনের সহিংস ও বিদ্বেষমূলক ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার ফলস্বরূপ এমন একটি প্রতীকী আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। ধর্মবাদীদের পক্ষ থেকে এখন দাবি করা হচ্ছে, উক্ত নারীমূর্তিটি নাকি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বোঝাতে নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ, তাদের ধারণায় যদি সেটি শেখ হাসিনার হয়, তাহলে তার উপর নির্যাতন গ্রহণযোগ্য হয়ে পড়ে। অথচ, একই ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো একসময় শেখ হাসিনাকেই ‘কওমি জননী’ বা ‘মা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলো। তাহলে, তারা নিজের ‘মা’-র মূর্তি বানিয়ে তার উপর প্রকাশ্যে নির্যাতন চালিয়েছে? বিষয়টি রাজনৈতিক ভণ্ডামির উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
এখানে একথা মনে রাখা জরুরি, মূর্তিটিতে শেখ হাসিনার কোনো নাম, ছবি, কিংবা সরাসরি ইঙ্গিত ছিল না। অতীতে সরকারবিরোধী ভাস্কর্য ও ব্যঙ্গচিত্রে এরকম নাম বা প্রতীক যুক্ত থাকলেও, এই মূর্তিটি ছিল সম্পূর্ণ অনামিকা। সুতরাং ধর্মবাদীদের দাবি তথ্যভিত্তিক নয়, বরং তাদের রাজনৈতিক বিদ্বেষকে আড়াল করার একটি চাল। এই দাবি মিথ্যা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রমাণহীন। সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার মুখে , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল টিম জানান, কয়েকজন ব্যক্তি বৃহস্পতিবার এই কুশপুতুল রাজু ভাস্কর্যের পাশে রেখে যায়। সেটি শেখ হাসিনার প্রতিকৃতি বলে সবাই জানে। শনিবার হেফাজতের কর্মীরাও এটাকে শেখ হাসিনার কুশপুতুল ভেবেই জুতা মেরেছে। ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমেদ বলেন, ‘জাগ্রত জুলাই নামে একটি সংগঠন শেখ হাসিনার কুশপুতুল ফাঁসিতে ঝুলিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শনিবার এটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
একজন নারী কিংবা পুরুষ, মানুষ হিসেবে কারো মর্যাদাহানিকর ব্যবহার কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিচার না হওয়া পর্যন্ত কাউকে অপরাধী বলা যায় না। আর অভিযুক্ত হলেও তার প্রতি সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সহিংসতা চালানো এক ধরনের ফ্যাসিবাদী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা যদি সত্যিকার অর্থে মানবিক সমাজ চাই, তাহলে অপরাধী বা নিরাপরাধ—সবার জন্যই ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। বিচারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নামে প্রকাশ্যে নারীর প্রতীকের উপর আক্রমণ কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য নয়। আজকের বাস্তবতা ভয়াবহভাবে জটিল। নারী অধিকার, সংস্কার, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এসব কেবল কথার ফুলঝুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলি, অন্যদিকে ধর্মান্ধ শক্তিগুলোর কাছে মাথা নত করি। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় আমাদের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল, আজকের বাস্তবতায় তা ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত হয়েছে।
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় আমরা শুনেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের গান, গণসংগীত, স্লোগান, সাহিত্য, সংস্কৃতি। সেসব ছিল আমাদের চেতনার মূল চালিকাশক্তি। কিন্তু আগস্টের পর থেকে সেই সাংস্কৃতিক স্ফুরণ আর চোখে পড়ে না। ধর্মীয় পরিচয়ের নামে যে নতুন সমাজ বিনির্মাণের কৌশল গৃহীত হয়েছে, তার মূলে রয়েছে একটি মৌলিক সংকট: ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক ইসলাম। এই মৌলবাদী শক্তির উত্থান হঠাৎ করে হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে—কখনো ভোটের স্বার্থে, কখনো রাজপথে শান্তি বজায় রাখার নামে। শেখ হাসিনা সরকার যখন হেফাজতের সাথে আপস করলো, তখন থেকেই মৌলবাদীদের সাহস বেড়ে গেল। তারা জানলো, রাষ্ট্র তাদের থামাবে না। বরং সুযোগমতো তাদের কাজে লাগাবে। আজ সেই ব্যবস্থার ফল ভোগ করছে গোটা সমাজ।
আমরা যদি প্রশ্ন না তুলি—কেন এখন এত মোল্লা-মুনশি-টুপি? কেন তারা হঠাৎ করে এত সংগঠিত, এত আত্মবিশ্বাসী? তবে বুঝে নিতে হবে, তারা একা নয়। তারা রাষ্ট্রের ভেতরকারই আরেক রূপ। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত অংশের মধ্যেই তাদের স্মার্ট সংস্করণ লুকিয়ে আছে। এনসিপির হাসনাত যখন নারীনীতি বিরোধী সমাবেশে বক্তৃতা দেন, তখন বুঝতে বাকি থাকে না, তারা কেবল ধর্মীয় নয়—বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইটিও দখলে নিতে চাইছে।
তাদের দাবিকৃত ‘বৈষম্যহীনতা’ আজ কোথায়? তারা কি কোনো অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির চর্চা করছে? না, বরং তারা ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যকে আরও সুসংগঠিত করছে। এদের কাছে গণতন্ত্র, আইনের শাসন, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য—সবই হাস্যকর একটি ভ্রান্ত ধারণা। এদের কাছে নারী মানে ঘরের কোণে থাকা, পুরুষতন্ত্রের নির্দেশ মানা, এবং প্রগতির পথ রুদ্ধ করা।
লড়াইটা এখন আর শুধু রাজনৈতিক নয়, এটা একটি সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে। সেই আন্দোলন হবে ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক, নারীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। সামনে দুটি পথ—একদিকে ধর্মান্ধতার রাজনীতি, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক জাগরণ। আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, আমরা কোন পথ বেছে নিই।